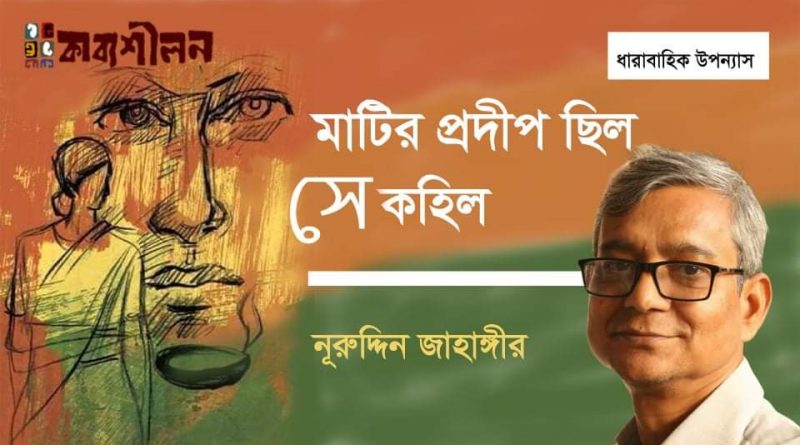উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল ।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ।। পর্ব ছয়
- উপন্যাস// মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল// নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর// এক
- উপন্যাস// মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল// নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর// দুই
- উপন্যাস// মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল// নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর// তিন
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিলো, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব চার
- উপন্যাস// মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল// নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর// পাঁচ পর্ব
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল ।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ।। পর্ব ছয়
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল ।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ।। পর্ব সাত
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব আট
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব নয়
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল ।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব দশ
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ।। পর্ব এগারো
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব বারো
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।।পর্ব তেরো
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। চৌদ্দ
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব পনরো
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব ষোল
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব সতেরো
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। পর্ব আঠারো
- উপন্যাস।। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল।। নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।। শেষ পর্ব
গাছপালা ঘেরা পতিসর গ্রামটা যে এত ঘনবসতিপূর্ণ বাইরে থেকে সেটা বোঝাই
যায় না। গ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসাদ করিমের মনে হচ্ছে একই
পরিবারের অনেকগুলো মানুষ যেন কোনো এক অজানা সময়ে এখানে এসে
একবারে যে যার মতো ঘর তুলে বসত করতে শুরু করেছিল। যেন আদিম
সমাজের কোনো গোত্রপ্রধান উর্বর জমির সন্ধানে এখানে এসে প্রথম বসতি স্থাপন
করেছিল। তারপর পরিবার ভাগ হয়েছে, সন্তানদের নতুন নতুন পরিবার গড়ে
উঠেছে, সংখ্যা বেড়ে বেড়ে একদিন একটা পাড়া, তারপর গ্রাম হয়ে গেছে।
আওলাদ বাড়তে বাড়তে কোনো সীমানা চিহ্নিত না করেই যে যার মতো ঘর তুলে
বসত করতে শুরু করে। মানুষ বাড়লেও তাদের আয় তেমন বাড়ে নি। অধিকাংশই
নিম্ন আয়ের পরিবার বোঝা যায়। ঘর দেখে আন্দাজ করা যায় কার আর্থিক
সচ্ছলতা কেমন। যাদের আগের থেকে সামর্থ্য আছে তাদের মাটির দেয়ালের
উপর টালির ছাদ দিয়ে ঘর। কোনো কোনো ঘর খুব উঁচু। ভেতরে উপরের দিকে
যে আরো একটি মাচার মতো কিছু আছে বাইরে বেরিয়ে থাকা কাঠের রোয়া
দেখে বোঝা যায়। এতে হয়ত ধান, পাট বা অন্য কোনো শস্য মজুদ করা হয়।
মাটির দেয়াল যে বেশ মজবুত সেটাও বাইরে থেকেই আন্দাজ করা যায়। আর দু-
একটি ঘর পাকা, সাদামাটা ইটের গাঁথুনি দেয়া দালান। মাটির দেয়ালের সংগে
তেমন তফাৎ নেই, ধরন একই। আসাদ আন্দাজ করতে পারছে এসব নতুন
দালান-ঘর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু ওর মনে যে
পুরো গ্রামটির বসতি সম্পর্কে একটি একক বংশধারার ধারণা জন্মেছে সেটা কী
ঠিক? এখানে তো বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের বসবাস এক সঙ্গেই আছে।
বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই এমন আছে। আর এদেশের মাটিতে যে বাঙালী
জাতিসত্তা কালক্রমে গড়ে উঠেছিল সেই জাতির লোকজন বৈদিক ধর্মের অনুসারী
হয়েছিল আর্যদের আগমনের পরে। এর আগে এখানে স্থানীয় কোনো ধর্ম নিশ্চয়
ছিল। বৌদ্ধ ধর্মমতও এখানে বিস্তার লাভ করেছিল। খুব কাছেই বৌদ্ধদের
বিদ্যাপীঠ পুন্ড্র নগর গড়ে উঠেছিল। আর কৃষিজীবী মানুষগুলো এতই নিরীহ
আর শান্ত ছিল যে, যে যখন শাসন করেছে তার ধর্মমত রাজধর্ম বলে মেনে
নিতেও দ্বিধা করে নি। যুদ্ধ এই জাতির রক্তের মধ্যে কখনো ছিল না। তবে এরা
সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে সব সময় চেষ্টা করেছে। হাঁটতে হাঁটতে আসাদ
করিমের মনে মানুষের সামাজিক বন্ধন সম্পর্কে কৌতূহল জেগে উঠছে। কিন্তু এ
রকম প্রশ্ন করা সঙ্গত নয়, বিশেষ করে একজন হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতে যাবার
পথে এ প্রশ্ন শিষ্টাচার বহির্ভূতও বটে। তারপরও একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে যাওয়ার
আগে তার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানার আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক বলেই সে মনে করছে।
সে প্রসঙ্গটি অন্যভাবে তোলে। পতিসর গ্রামের সব মানুষ যেন এক পরিবারের সদস্য।
এমনটি কেন মনে হলো?
সব বাড়িঘর এমনভাবে মিলেমিশে আছে, আলাদা করা যায় না। ঘর দিয়ে, নির্মাণের ধরন আর সব বাড়ির
উপর দিয়েই তো আমরা হেঁটে হেঁটে এলাম। কোনোটা আলাদা করা নেই। মানুষের মধ্যে যে খুব মিল─
আন্দাজ করা যায়।
একসময় হয়তো তাই ছিল। এখন ঘর এক হলেও মন পৃথক।
যাক সেকথা, আদতে এখানে উঁচু ভূমির খুব অভাব। বিলের ধারে বসতি।
চলনবিল এখান থেকে আরো উত্তরে, রানীনগর থেকে শুরু হয়েছে।
বিল থাকলে তো এখানে মৎস্যজীবী থাকার কথা─ আছে নিশ্চয়।
মৎস্যজীবী এখন নামমাত্র আছে। মৎস্যজীবীরা আর মাছের উপর নির্ভর
করে জীবন ধারণ করে না।
তারা অন্য কাজ করে।
তারা কী কাজ করে?
তারা যে যা পারে সেটাই করে। কেউ মজুর, কেউ বর্গা করে, কেউ ব্যবসা আর কেউ
বা চাকরি-বাকরিও করে। যেমন, আমি স্কুলে মাস্টারি করি।
আপনার পূর্বপুরুষ মৎস্যজীবী ছিলেন?
হ্যাঁ, আমরা জলদাস। যাকে বলে কৈবর্ত। কৈবর্তদের কোথাও কোথাও ধীবর
বলেও অভিহিত করা হয়।
এখান থেকে পুন্ড্রনগর তো দূরে নয়, তাই না?
মাত্র বিশ মাইল।
আপনারা তাহলে এক গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকার।
আপনি কি ঠাট্টা করছেন?
ঠাট্টা করবো কেন? কৈবর্তরাই তো এদেশে প্রথম গণজাগরণ এনেছিল,
এখানকার ধীবর জনগোষ্ঠিই তো তাদের নেতা দিব্যকের নেতৃত্বে এদেশে রাজতন্ত্র উৎখাত
করেছিল।
আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।
দিব্যকের কথা জানেন না?
দিব্যক?
দিব্যকের নেতৃত্বে মৎস্যজীবী কৈবর্তরা যাদের ধীবর বলা হতো—তারা
গৌড়ের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তারা মহিপালকে হটিয়ে তাদের
নেতা দিব্যককে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। গণজাগরণের সেই স্মারক এখনো ধীবর
দীঘির মাঝখানে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।
পত্নিতলার ধীবর দীঘিতে সেই স্তম্ভ তো আমিও দেখেছি। কিন্তু আপনি যা
বলছেন তা তো আমি কিছুই জানি না!
পন্তিতলার ধীবরদীঘিতে কৈবর্ত শাসনের স্মৃতিচিহ্নই আপনি দেখেছেন।
পত্নিতলার শশাষ্ক বাবু বহির্দরোজার কাছে এসে ডাকলেন, আমরা এসে পড়েছি।
দরোজা খোল, মা চাঁপা।
আসছি, বাবা।
ভেতর থেকে জবাব এল। আর তারপর দরোজাও খুলে গেল। একটি
তরুণীর চোখে আসাদের চোখ পড়ল।
ইনি আসাদ করিম। আমাদের স্কুলের নবীন শিক্ষক।
আদাব, আসুন।
চাঁপা যেন রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে সব মেয়ের নাম পাওয়া যায় শ্যামলী, চাঁপা
ইত্যাদি ওদেরই একজন। ওরকমই চেহারা, পোশাকাদি। তামাটে
মুখে সত্যি যেন চাঁপা ফুলের আভা ছড়িয়ে রয়েছে।
এত বেলা করে এলে ভদ্রলোকের কী অবস্থা করে দিলে বল দেখি। আর
এদিকেও ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।
কী আর করব। ভদ্রলোকের জন্যই তো বিলম্ব হলো। আমি মনে করলাম
প্রথম দিন, আজ হয়ত তিনি ক্লাসে যাবেন না। অবশ্য প্রথম দিনেই ছাত্র-
ছাত্রীদের মন জয় করে ফেলেছেন।
গুণী মানুষের বেলায় তাই হয়।
আমাকে লজ্জা দিবেন না, স্যার। আমি ওদের আজ পড়াই নি। কেবল
পরিচিত হবার জন্য গল্প করছিলাম।
শিশুরা যা বলে যথার্থই বলে, বানিয়ে বা বাড়িয়েও বলে না। তারা মানুষ
চিনতেও ভুল করে না। সঠিকভাবেই মানুষকে মূল্যায়ন করে। আসুন, খেতে
খেতে কথা বলি।
কতদিন পর এরকম অনেকগুলো ব্যঞ্জন একসঙ্গে দেখল- আসাদ মনে
করতে পারছে না। সে চোখ ফেরাতে পারছে না। সে আগে
ভাবতেও পারে নি খাওয়া মানে কেবল ক্ষুধা মেটানো নয়, দেখার তৃপ্তিও বটে।
আমি ভালো রান্না করতে পারি না। আমার মা পারতেন। আমাকে শেখার
সুযোগ না দিয়ে তিনি স্বর্গে চলে গেলেন। কী আর করা। নিন শুরু করুন।
হ্যা, চাঁপা খুবই দুর্ভাগা মেয়ে। ওকে আমরা কেউ ওর মতো বড় হতে
দিতে পারি নি। ওর মা মারা যাওয়ার পর মায়ের দায়িত্বটাও ওকেই নিতে হলো।
তা না হলে আমার যে কী হতো! আর ছেলেটাকে কে মানুষ করতো?
আপনার ছেলেটা কোথায়?
নিখিল ভার্সিটিতে। ফিজিক্সে অনার্স পড়ছে। মাত্র ফার্স্ট ইয়ার।
বেশ তো।
মেয়েটা আইএ পাশ করে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেয়ে মাস্টারি করছে। কত
করে বললাম, আমি চালিয়ে নিতে পারব। তুই পড়ালেখাটা কর। তারপর দেখা
যাবে। সে বলল, আমাকে রেখে সে পড়ালেখা কেন, বিয়ে করেও শ্বশুরবাড়ি যাবে
না। শুনুন─ পাগলী মেয়ের কথা।
বাবা, মেয়ের এত বদনাম তুমি আগে তো করতে না। তা ছাড়া ইনি
অতিথি। এসব শুনে আমাদের সম্পর্কে ধারণা কী হবে?
আমি তো মিথ্যে কিছু বলছি না।
আচ্ছা, থামো, ভদ্রলোককে খেতে দাও। তুমিও খাচ্ছো না, তিনিও হাত
গুটিয়ে বসে আছেন। একজন কথা বললে অন্যজন কী করে আহার করবেন?
ও, আমি সেকথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ছোটো মাছ আরো একটু নিন।
এটা পুদিনাপাতা দিয়ে ঝোল। আর এটা সজনেডাঁটা। নিতে হবে কিন্তু। কনকচাঁপা বলল।
নেবো। এতগুলো ব্যঞ্জণ একপাতে খাওয়া সম্ভব? সজনে ডাঁটা, ডালের বড়ি লোভ সামলে
রাখা মুশকিল।
লোভ সামলানোর দরকার নেই, ইচ্ছে মতো খেতে থাকুন।
জানিস মা, আসাদ সাহেব আজ আমাকে এক নতুন ইতিহাস শোনালেন।
তাও সামান্য একটু। শূদ্র বলে যাদের মানুষ নিচে ফেলে রাখে তারাই নাকি
এদেশে গণজাগরণের পথিকৃৎ। তারাই নাকি প্রথম এদেশে জনগণের অধিকার
প্রতিষ্ঠা করেছিল।
জাতপাত কিছু না, বাবা। কর্মে নয়, যারা আচরণে নিচু তারাই নিচুজাতের।
জাত নয়, মানুষই আসল। আর সব ভুয়া, ভাঁওতাবাজি। মানুষ কখনো জাতের
কারণে নিচু হতে পারে না। জাতফাতের ইতিহাস তো উপমহাদেশের। আর
অন্যান্য দেশে মালিক আর শ্রমিক আছে, জাত নেই, বর্ণ নেই। এসব তো
মানুষকে নিচে ফেলে রাখার কৌশলমাত্র। আপনি কী বলেন?
ঠিকই বলেছেন, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’, মানুষ জেগে উঠলেই সবকিছু
বদলে ফেলা সম্ভব হয়।
আসাদ সাহেব ঠিকই বলেছেন। বাবা, তুমি কৈবর্ত জাগরণের কথা জানো
না? এ তো আমাদেও নিজেদেরই ইতিহাস।
তুই জানিস! কখনো বলিস নি তো?
বলে আর কী হবে? এখন জাগরণের যুগ নয়, ক্ষমতারোহণের যুগ।
গণতন্ত্রের নামে মানুষের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য
জনগণের ভোট চাই, আর ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে কাঁচকলা দেখাই।
আপনি খুব ভালো বলেছেন। আর যা অবশ্যই বলা দরকার─আপনার রান্না
খুব ভালো হয়েছে।
আপনিও অন্যদের মতোই বললেন। মেয়েদের রান্নার গুণ সকলেরই চোখে
পড়ে। এ জন্য রান্নার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি রান্নার চর্চা করি
না।
চর্চা না করেই এত ভালো! যদি চর্চা করতেন তাহলে কেমন হতো সেটা
ভাবতেই পারছি না।
আচ্ছা, এ প্রসঙ্গ থাক। রান্না নিয়ে বেশীক্ষণ আমি কথা বলতে পারি না।
শুনেছি, আপনি সাহিত্যের লোক। লেখালেখি করেন। কী লিখেন, গল্প না কবিতা?
গল্প, ছোটোগল্প।
ছোটোগল্প? ছোটোগল্প লেখাই তো কঠিন। এখন তো ভালো ছোটোগল্প চোখেই
পড়ে না। দৈনিকে যেসব গল্প ছাপা হয় সেগুলো বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না আর
গল্পও মনে হয় না। পড়লে মনে হয় খুব কষ্ট করে একটা কিছু বানানোর কসরত
করা হয়েছে। সেখানে মানুষ আছে তার অবয়ব নেই, জীবনের কোনো প্রতিফলন
নেই। যেন চরিত্রগুলো মানুষ নয়, লেখকের বানানো পুতুলমানব। কেন এখনকার
লেখকরা রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর-মানিক বন্দোপাধ্যায়ের
মতো গল্প লিখতে পারেন না? বুঝতে পারি না।
বর্তমান লেখকদেরও কেউ কেউ ভালো গল্প লিখছেন। আবার কারো কারো ভালো না
লিখতে পারার পেছনে কারণও রয়েছে।
কী কারণ?
এখন রবীন্দ্রনাথ-তারাশঙ্করদের কাল নয়। এমন কি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের
কালও নয়। তাঁদের গল্পে সামন্তবাদী চরিত্র আর সে সময়ের অত্যাচার-শোষণের
দিকটি ফুটে উঠত। প্রজাস্বত্বের অনুপস্থিতি আর জমিদারের ভোগবিলাসী
জীবনচিত্রের পাশাপাশি কৃষকদের দুর্দশা সেই সময়ের লেখকদের লেখার মূল
উপজীব্য ছিল। অবশ্য শরৎচন্দ্র ধর্মীয় গোঁড়ামী আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের
প্রেক্ষাপটে নারীজীবনের করুণ ছবি খুবই মর্মস্পর্শী করে তাঁর গল্পে তুলে
এনেছেন। আমাদের যুগটা তখনকার যুগের মতো নয়। সামন্তবাদী সমাজ ও
অর্থনীতি পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। পুঁজিবাদের ঢেউ এখানেও এসে উপস্থিত
হয়েছে। এখন আমাদের সমাজটাকে দেশীয় আর বহুজাতিক পুঁজিই নিয়ন্ত্রণ
করছে। ত্যাগের চাইতে ভোগ বাড়ানোর নীতিই বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে,
এখনকার গল্পকারদের উপরও পুঁজিবাদের ভোগবাদী প্রভাব পড়ছে। পণ্য যখন
বাজারে আসছে মানুষও তা ভোগের জন্য ব্যাকুল আর কখনো বা বেপরোয়া হয়ে
উঠছে। এর প্রতিফলনই বর্তমান লেখকদেও রচনায় ধরা পড়ছে। এখন লেখকরা
আর গ্রাম বা কৃষকের সমস্যা নিয়ে ভাবে না, শহর এবং নগরজীবনের সঙ্কট নিয়ে
ভাবে। তারা নাগরিক জীবনের অন্ধকার দিক নিয়ে গল্প লিখতে পছন্দ করে।
অথচ সেটা ফুটিয়ে তুলতে তারা পারে না। কারণ, আমাদের শহর এখনো শহর
হয়ে উঠেনি। আর শহরের বাসিন্দা এখনো গ্রাম ভুলে যেতে পারেনি। তাদের এক
পা শহরে আরেক পা এখনো গ্রামে। আবার নতুন অর্থনীতি আমাদের যান্ত্রিক
করে তুলছে। আমরা যন্ত্রের পেছনে ছুটছি। অথচ যান্ত্রিক সভ্যতায় এখনো
পৌঁছাতে পারছি না। তবু আমরা সবকিছু যন্ত্রের মতো করে দেখি, যা চাই যন্ত্রের
মতো নিখুঁত করে পেতে চাই। জীবন আসলে নিখুঁত নয়, জীবনে ভুলত্রুটি আছে,
থাকবে। জীবনকে যান্ত্রিক করে যাপন করা যায় না। যন্ত্রের সাথে তাল মিলাতে
গিয়ে আমাদের আচরণ যেমন যান্ত্রিক করে ফেলেছি, তেমনি ভাষাকেও যান্ত্রিক
করে ফেলেছি। সব কিছু বাইরে থেকে আনা সূত্র আর মডেলের মাধ্যমে পেতে
চাই। জীবনের চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি সবই আমরা তত্তে¡র মাধ্যমে প্রকাশ করতে
চাই। হয়তো বলবেন, এদেশটা যে এখনো কৃষিনির্ভর, যন্ত্রনির্ভর হয়ে যায় নি সেটা
তারা ভুলে যায় কেন। কিন্তু একটা বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে যে, বাংলাদেশ
পিছিয়ে থাকলেও পৃথিবীটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আর সেসব অগ্রসর কিংবা
অগ্রগতির বিচ্যুতিজাত চিন্তার ঢেউ মুক্ত বাতায়ন ভর করে এখানে এসে লাগছে।
সেসব কিছু আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করছে। আমরা নতুন কিছু করতে গিয়ে,
বাইরের সবকিছুর অন্ধ অনুকরণ করছি। এটা ঠিক যে আমাদের এগিয়ে যেতে
হলে সময়কে বুঝতে সময়ের চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে হবে। পৃথিবীর কোথায়
কী ঘটছে তার খোঁজ-খবর রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যদি সে যুগে, তাঁর যৌবনেই
ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গে পরিচিত না হতেন, তাহলে তিনি মাতৃভূমিকে, বিশেষ
করে পিছিয়ে পড়া বাংলাকে এত তাড়াতাড়ি চিনতে পারতেন না। তখন তথ্যের
প্রবাহ এখনকার মতো ছিল না। তাই তাঁকে ইউরোপে গিয়ে আধুনিকতার সঠিক
রূপ কী সেটা বুঝতে হয়েছিল। দেখে, জেনে আর বুঝেই দেশমাতৃকার কথা ভেবে
স্বদেশে ফিরেও এসেছিলেন। তবু তাঁকে অনেকেই, এমন কি তাঁর স্বকালেই বুঝতে
পারেন নি, পরবর্তীকালেও না, এখনো যে সকলেই তাঁর আসল মননশীলতার
জায়গাটি স্পর্শ করতে পারেন, তাও নয়। যাক, যে কথা থেকে শুরু করেছিলাম,
আমি আসার আগে আশরাফ স্যার খুব মূল্যবান কিছু কথা বলেছিলেন।
কী বলেছেন?
বলেছিলেন, আমাদের লেখকগণের অভিজ্ঞতারও অভাব রয়েছে। আর
বর্তমান লেখকদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা রাতারাতি বিখ্যাত হতে
চায়। রাতারাতি বিখ্যাত হতে গিয়ে নতুন চমক সৃষ্টি করতে চায়। তাদের
জীবনের অভিজ্ঞতা স্থিত হওয়ার আগেই হয়তো পাশ্চাত্যের অন্যকোনো ধারণার
সাথে তাদের পরিচিতি ঘটে। তখন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বদলে নতুন চমক
দেখানোর জন্য বিদেশী চিন্তাবিদদের কোনো একটি তত্তে¡র অনুকরণে আর কিছু
শব্দের উলটপালট ব্যবহার করে একটা গল্প ফেঁদে বসে। আর এই অদ্ভুত গল্পটি
দেখে আমাদের চোখে তখন ধাঁধাঁ লেগে যায়। আমরা মানে, তাদের বন্ধু-বান্ধব
শুভাকাক্সক্ষী সঠিক মূল্যায়ন না করে, প্রকৃত অর্থে সমালোচনা না করে বাহবা দিতে
শুরু করি। এতে তারা নিজেদেরকে আর বুঝতে পারে না। কিন্তু কিছুদিন পর
তাদের আর প্রকৃত সাহিত্যের মাঠে খুঁজেই পাওয়া যায় না। কারণ, একই চমক
তারা বারবার দেখাতে পারে না।
অভিজ্ঞতা অর্জনের বিকল্প যেহেতু কিছু নাই, তাহলে হারিয়ে যাওয়ার আগে
হলেও তারা সেটা অর্জন করতে চেষ্টা করে না কেন?
অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও তাদের হয় না।
কেন?
বর্তমানে লেখক কারা হচ্ছে? তাদের অবস্থান কোথায়– সেটা ভেবে দেখলেই
বোঝা যাবে কেন অভিজ্ঞতার এত অভাব। বর্তমানে যারা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা
করে তারা শহরেই বেড়ে ওঠে। সংস্কৃতি-সাহিত্য চর্চার জন্য যে সময় প্রয়োজন
সেটা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সর্বক্ষণ ছুটে বেড়ানো ব্যস্ত
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের অর্থের থলি ঠনঠন হলেও অভিজ্ঞতার ঝুলি
বেশী পূর্ণ। তারা লিখলে ভালো লিখতে পারেন। কিন্তু সেই সময় তাদের হয় না।
তাহলে কারা লেখার সময় পান? শহুরে মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের সন্তানরা।
মধ্যবিত্ত সবসময় অর্থ আর উচ্চবিত্ত ক্ষমতার পেছনে ধাওয়া করে। ফলে তারা
তাদের পরিবার ও সন্তানদেরও সময় দিতে পারে না। তাদের সন্তানদের
অধিকাংশই মাটি আর মানুষ থেকে দূরে থাকে। নিজেদের মনের মধ্যে একটা
কল্পনার জগতও তারা তৈরি করে। কিন্তু জনবিচ্ছিন্নতার কারণে তারা সাধারণ
মানুষের মতো ভাবতে পারে না। এদের কেউ শখের বশে, কেউ কেউ বৃত্ত থেকে
বেরিয়ে এসে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরাই লেখালেখি করে। যা লেখে
তাই আবার ছাপাও হয়। শুধু ছাপা নয়, সঙ্গত কারণে মিডিয়াও তাদের পৃষ্ঠপোষক।
ফলে মিডিয়াতে যা প্রচার হয়, সেখানেও জীবন খুঁজে পাওয়া যায় না। যাক, অনেক
কথা বললাম। সবকথার আপনার মতের মিল নাও হতে পারে।
মতের মিল অমিল বড় কথা নয়। এমন করে কারো কথা আমার শোনাও হয় না।
সময় পেলে আসবেন। সাহিত্যের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে।
আপনার সাথে পরিচয় হয়ে ভালো লাগল।
শশাঙ্কবাবু এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন, আমি তো এতক্ষণ শুনলাম কেবল,
বুঝিনি কিছুই। মেয়েটা নাকি একটা-দু’টা কবিতাও লিখেছে। অবশ্য আমাকে দেখায় নি।
আমিও দেখতে চাই নি। আমি তো অঙ্কেও মাস্টার। এখনকার কবিতা দূরে থাক গদ্যও বুঝি না।
তোমাকে দেখানোর মতো হলে তো দেখাবো!
আমি যদিও কবিতা লেখার মতো কঠিন কাজ করতে পারি না। তবুও পিতার মুখে কন্যার
কাব্যকথা শুনে কবিতা শুনতে ইচ্ছে করছে।
ওসব ছাইভস্ম শোনানোর মতো কিছু নয়।
ঠিক আছে। ও কবিতা শোনাবে কি না সেটা কোনো বিষয় নয়। আপনি সময় করে আসবেন।
আমাদের ভালো লাগবে।
ধন্যবাদ, শুভসন্ধ্যা।
শুভসন্ধ্যা।
ফিরে আসতে আসতে আসাদের মনে হচ্ছিল─ গ্রামের মানুষ তাহলে বাঙালীর চিরায়ত
আতিথেয়তার সংস্কৃতিটা এখনও লালন করে চলেছে। এখনও কত সহজেই না
এরা অচেনা মানুষকেও আপন ভাবতে পারে!