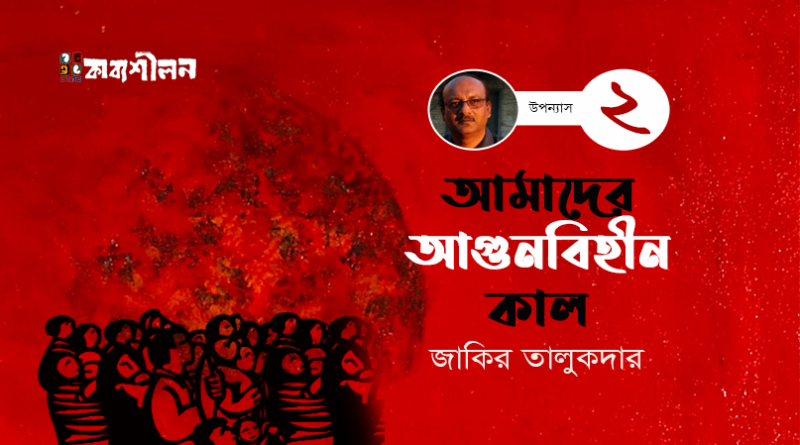ধারাবাহিক উপন্যাস // আমাদের আগুনবিহীন কাল // জাকির তালুকদার // দ্বিতীয় পর্ব
- উপন্যাস// আমাদের আগুনবিহীন কাল//জাকির তালুকদার//প্রথম পর্ব//
- ধারাবাহিক উপন্যাস // আমাদের আগুনবিহীন কাল // জাকির তালুকদার // দ্বিতীয় পর্ব
- ধারাবাহিক উপন্যাস / আমাদের আগুনবিহীন কাল / জাকির তালুকদার / তৃতীয় পর্ব
- ধারাবাহিক উপন্যাস /আমাদের আগুনবিহীন কাল /জাকির তালুকদার /চতুর্থ পর্ব
- ধারাবাহিক উপন্যাস // আমাদের আগুনবিহীন কাল // জাকির তালুকদার // পঞ্চম পর্ব
- উপন্যাস // আমাদের আগুনবিহীন কাল // জাকির তালুকদার // ষষ্ঠ পর্ব
- উপন্যাস// আমাদের আগুনবিহীন কাল// জাকির তালুকদার// সপ্তম পর্ব
- উপন্যাস// আমাদের আগুনবিহীন কাল// জাকির তালুকদার// পর্ব আট
- উপন্যাস // আমাদের আগুনবিহীন কাল // জাকির তালুকদার // পর্ব নয়
- উপন্যাস // আমাদের আগুনবিহীন কাল // জাকির তালুকদার // পর্ব দশ
- উপন্যাস।। আমাদের আগুনবিহীন কাল।। জাকির তালুকদার।। পর্ব এগারো
টিএইচও ডাক্তার খলিলুর রহমান মানুষটা খারাপ না, কিন্তু একঘেয়েমিতে আক্রান্ত। ২৪ বছর ধরে সরকারি চাকরি করে এতদিনে মেডিক্যাল অফিসার থেকে থানা হেলথ অফিসার হয়েছেন। তিনি জানান, তার ক্লাসমেট, যারা প্রশাসন ক্যাডারে গিয়েছে, তারা পাঁচ বছর আগেই ডিসি হয়ে গেছে। তিনি এখনও পড়ে আছেন গ্রামে-গঞ্জে। এই হচ্ছে মেডিক্যাল ক্যাডারের অবস্থা। আসলেই ডাক্তারদের সরকারি চাকরি করা উচিত নয়। তবে থানা লেভেলে চাকরি করে করে তিনি ঢাকাতে ফ্ল্যাট কিনেছেন, গাড়িও একটা আছে, দেশের বাড়িতে ত্রিশ বিঘার ওপর জমি কিনেছেন বাগান বানানোর জন্য বাড়িও একটা বানিয়েছেন দোতলা। এক ছেলে এবং এক মেয়ে। একজন মেডিক্যালে পড়ছে, আর একজন বেসরকারি ইউনিভার্সিটেতে বিবিএ। জেলা শহরে থাকলে প্র্যাকটিস কিছুটা বেশি হতো। কিন্তু কী আর করা। নিজের সম্পর্কে এই পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন তাকে এখানে আসার পরদিনই। তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন- ‘তা ইমরুল করিম তুমি কেন এই রিমোর্ট উপজেলায় এলে? ধরাধরি করে একটু ভালো জায়গায় পোস্টিং নিতে পারলে না? মামা-চাচা নাই? তা বাবা কী করেন?’
সে উত্তর দেয়- ‘ব্যবসা।’
‘কীসের ব্যবসা?’
‘এই আর কী।’
সে এর চেয়ে বেশি বলে না। ডা. খলিলও বেশি চাপাচাপি করেন না। আসলে অন্যের কথা কম শুনতে শুনতে তার অভ্যেস হয়ে গেছে। নিজের কথা বেশি বলতেই আরাম পান। সেই অভ্যাসবশেই আবার বলে ফেলেন- ‘কী দরকার ছিল এই ধ্যাদ্ধেরে গোবিন্দপুরে আসার! ইয়াং ছেলে। সময় কাটানোর উপায় নাই। কথা বলার মতো মানুষ খুঁজে পাবে না। মেলামেশা করা তো দূরের কথা। কীভাবে থাকবে এখানে!’
বাবাও এমন কথাই বলেছিল। ‘ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা ছিল- পড়েছ। এখন চাকরি করতে গ্রামে যাওয়ার কী দরকার? আমাদের ফার্মেই কত ডাক্তার চাকরি করছে। তুমি চাইলে অ্যাপোলো বা স্কয়ারে বা ইউনাইটেডে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া চাকরির দরকারই বা কী। অনারারি খাতায় নাম লিখিয়ে পিজি বা ডিএমসিতে যাতায়াত করো। দুই বছর পরে এমডি বা এফসিপিএস করতে ঢোকো। কিংবা যদি এখনই চাও, চলে যাও ইংল্যান্ডে। এমআরসিপি বা এফআরসিএস করে এসো। বিলাতি ডিগ্রি বলে কথা। সবাই সেলাম ঠুকবে। আর যদি সরকারি চাকরিই করতে চাও, জয়েনিং দেখিয়ে ডেপুটেশন করে দিচ্ছি ঢাকার কোনো হাসপাতালে। মোট কথা গ্রামে যাওয়ার দরকার নাই।’
কিন্তু সে তো সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল গ্রামে আসার, এবং এখানেই আসার। কবে থেকে? প্রপিতামহের ডায়েরিটা পড়ার পর থেকেই। এখানে পোস্টিং পেতে তার আদৌ কষ্ট করতে হয়নি। বরং যখন সে এখানকার পোস্টিংয়ের চিঠি হাতে নিয়ে ডিরেক্টরের অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল, তার দিকে করুণার চোখেই তাকিয়েছিল কেউ কেউ।
ডা. খলিলের কথা শেষ হলে সে আস্তে জিজ্ঞেস করেছিল- ‘আমি কি আউটডোরে যাব স্যার?’
একটু অবাক হয়েই তার দিকে তাকিয়েছিলেন থানা হেলথ অফিসার- ‘সে কী! প্রথম দিন এসেই কাজে নেমে পড়তে চাও! কাজ তো করতেই হবে। আমার এখানে থাকার কথা নয় জন ডাক্তারের। আছে পাঁচজন। তার মধ্যে দু’জন উপর মহলে ধরে ডেপুটেশন নিয়ে চলে গেছে ট্রেনিং পোস্টে। কাজ করতে করতে নাকের পানি চোখের পানি এক হয়ে যাবে হে! তাই বলছি আগে দুই-একদিন একটু ঘোরাঘুরি করো, ইচ্ছে হলে সিনিয়র তিন ডাক্তারের রুমে গিয়ে বসো, কথাবার্তা বলো তাদের সাথে, দ্যাখো তারা কীভাবে ম্যানেজ করে রোগীর পাল, তারপর তোমাকে রোস্টার দেব।’
খুবই বাস্তবসম্মত কথা। ইমরুল আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে যায় একই মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা সিনিয়র ভাই ডা. সেলিমের রুমের দিকে।
তবে তাকে কাজ শুরু করতে হয় সেই মুহূর্ত থেকেই।
সেলিম ভাই তাকে ঢুকতে দেখেই বলেন- ‘আইছো যহন, বইসা পড়ো মিয়া। আমারে যাইতে হবে ইনডোরে। ভাবতেছিলাম কারে রাইখা যাই। আমি উঠতাছি। তুমি আউটডোর সামলাও। এই চেয়ারেই বসো।’
অ্যাটেনডেন্ট ফরদু মিয়া প্রথম রোগীটাকে ঢুকিয়ে বসিয়ে দেয় তার টেবিলের বাম পাশের টুলে।
রোগীটার দিকে চোখ পড়তেই মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় ইমরুলের। তার সত্যিকারের কর্মজীবনের প্রথম রোগী। এর নাম-ঠিকানা-চেহারা তার মনে থাকবে চিরকাল। অন্তত মনে থাকা উচিত। রোগী আসলে একটা বাচ্চা। বছর আটেকের। তার মা তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে জড়োসড়ো কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে। যেন ডাক্তারের কাছে এসে, ডাক্তারকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে সে মহা অপরাধ করে বসেছে। তার সামনে রোগীর আউটডোর টিকিট রেখেছে ফরদু মিয়া। সেখানে হিজিবিজি দ্রুত অক্ষরে লেখা নাম- পাখি। বয়স নয় বৎসর।
বাচ্চা মেয়েটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায় ইমরুল। পলিমাটির মতো সোঁদা কালো মুখ। শুকনো। তবু কিশোরীসুলভ লাবণ্য মুছে যায়নি। হাত-পায়ের দিকে তাকালে বোঝা যায় অপুষ্টির শিকার মেয়েটি। তার মা-ও। তাদেরকে এত মনোযোগের সাথে লক্ষ করছে ডাক্তার, দেখে আরও যেন সিঁটিয়ে যায় মা-মেয়ে। ইমরুল একটু হাসি ফোটায় মুখে। অভয় মন্ত্রের মতো। নরম কণ্ঠে জানতে চায়- ‘কী হয়েছে? কী কষ্ট আপনার বাচ্চার?’
খালি ফিট লাগে। কয়দিন পর পর ফিট লাগে। এখন রোজ রোজ ফিট লাগে। দিনে দুই-পাঁচবারও ফিট লাগে।
ভুঁরু কুঁচকে ওঠে ইমরুলের। এপিলেপসি! মৃগি!
ভালো করে হিস্ট্রি নিয়ে আর পরীক্ষা করে মোটামুটি নিশ্চিত হয় ইমরুল- এটা মৃগিই।
কিন্তু সে ট্রিটমেন্ট দেবে কী করে? এটা তো বিশেষজ্ঞের কাজ। শিশু নিউরোলজিস্টের কাছে পাঠাতে হবে। তিনি একে ইইজি করাবেন, সিটি স্ক্যান করাবেন, এপিলেপসির টাইপ নির্ধারণ করবেন, তারপর চিকিৎসা দেবেন। মেডিক্যাল কলেজে ইন্টার্নশিপের সময় এটাই দেখে এসেছে ইমরুল। ফরদু মিয়াকে জিজ্ঞেস করে ‘এখানে কোনো শিশু বিশেষজ্ঞ আছেন?’
‘নাহ। তাক পাইতে হলে যাওয়া লাগবি জেলা সদরের হাসপাতালেত।’
পাখির মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ইমরুল- ‘মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবেন টাউনে?’
রোগীর মা বলে- ‘আমরা হদ্দ গরিব ছার! আপনেই যা হয় ওষুধ দ্যান ছার!’
‘একজন শিশু বিশেষজ্ঞ দেখালে ভালো হয়।’
বাচ্চার মা এবারও বলে- ‘আমরা হদ্দ গরিব ছার!’
‘কিছু পরীক্ষা করিয়ে আনতে পারবেন?’
পাখির মা আবারও বলে- ‘আমরা হদ্দ গরিব ছার!’
মনে মনে একটু অসহায় বোধ করতে থাকে ইমরুল। ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী এই রোগীকে তার রেফার করতে হবে। কিন্তু যা মনে হচ্ছে, একে রেফার করলে তার আর কোনো চিকিৎসা হবে না।
দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সে। তার কর্মজীবনের প্রথম রোগী। নিজের দায়িত্বেই এর চিকিৎসা করবে সে। স্লিপটা টেনে নিয়ে খস খস করে ওষুধ লেখে। বাড়িয়ে দেয় পাখির মায়ের দিকে। মুখে বলে- ‘এই ওষুধগুলো খাওয়াতে শুরু করেন। সামনের শনিবারে আবার নিয়ে আসবেন আমার কাছে।’
বাচ্চা কোলে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মহিলা। এই সময় ইমরুল ডাকে ফরদু মিয়াকে- ‘এই বাচ্চার ঠিকানাটা ভালো করে লিখে রাখেন তো ফরদু ভাই!’
স্পষ্টতই অবাক হয় ফরদু মিয়া। একটু বিরক্তও। বাইরে রোগীদের ঠেলাঠেলি। সে দরজা ছেড়ে নড়লেই সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে রুমের মধ্যে। এর মধ্যে এই হুকুম! তার বিরক্তি পরিষ্কার বুঝতে পারে ইমরুল। একটু অনুরোধের সুরেই বলে ‘আমি তো এই এলাকার কোনো গ্রাম বা পাড়ার নাম জানি না। আঞ্চলিক ভাষায় বললে বুঝতে পারব না। তাই আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।’
ফরদু মিয়া এই রকম ভাষা ডাক্তারদের কাছে শুনতে অভ্যস্ত নয়। সে একটু বেশিই ত্রস্ত হয়ে ওঠে। একটা স্লিপ টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে পাখির মাকে- ‘এই তোমার সোয়ামির নাম কী?’
‘হামিদ মিয়া।’
‘কুন পাড়াত বাড়ি?’
‘জিয়োনি পাড়া।’
‘আচ্ছা যাও। আমি চিনতে পারিছি।’
স্লিপটা যত্নের সাথে মানিব্যাগের ভাঁজে ঢুকিয়ে রাখে ইমরুল। তারপর মন দেয় পরের রোগীর দিকে।
তার পরেই আক্ষরিক অর্থেই রোগীর স্রোতে ভেসে অথবা ডুবে যায় ইমরুল। আসতেই থাকে রোগী। আসতেই থাকে। একটা একটা করে রোগী দেখছিল ইমরুল। ফরদু মিয়া এসে বলে- ‘এভাবে রুগি দেখলে ছার রাত তো হবিই, বিয়ানও হয়ে যাবার পারে!’
‘তাহলে?’
‘একসাথে চার-পাঁচজনারে ঢুকাই, আপনে এক কান দিয়া শুনবেন, এক হাত দিয়া লেখবেন, আর ফটাফট বিদায় করবেন। সব ছার এইভাবেই রুগি দ্যাখে ছার।’
ঈষৎ বিরক্তির সাথে ইমরুল বলে ‘আপনার ডিউটি টাইম শেষ হলে আপনি চলে যাবেন ফরদু ভাই। আমাকে জিজ্ঞেসও করতে হবে না। আমি যেভাবে দেখছি, সেভাবেই রোগী দেখে যাব।’
একটু যেন লজ্জিত হয় ফরদু মিয়া। তবে ডিউটি টাইমের পরে সে থাকবে না চলে যাবে, সে সম্পর্কে কিছু বলে না।