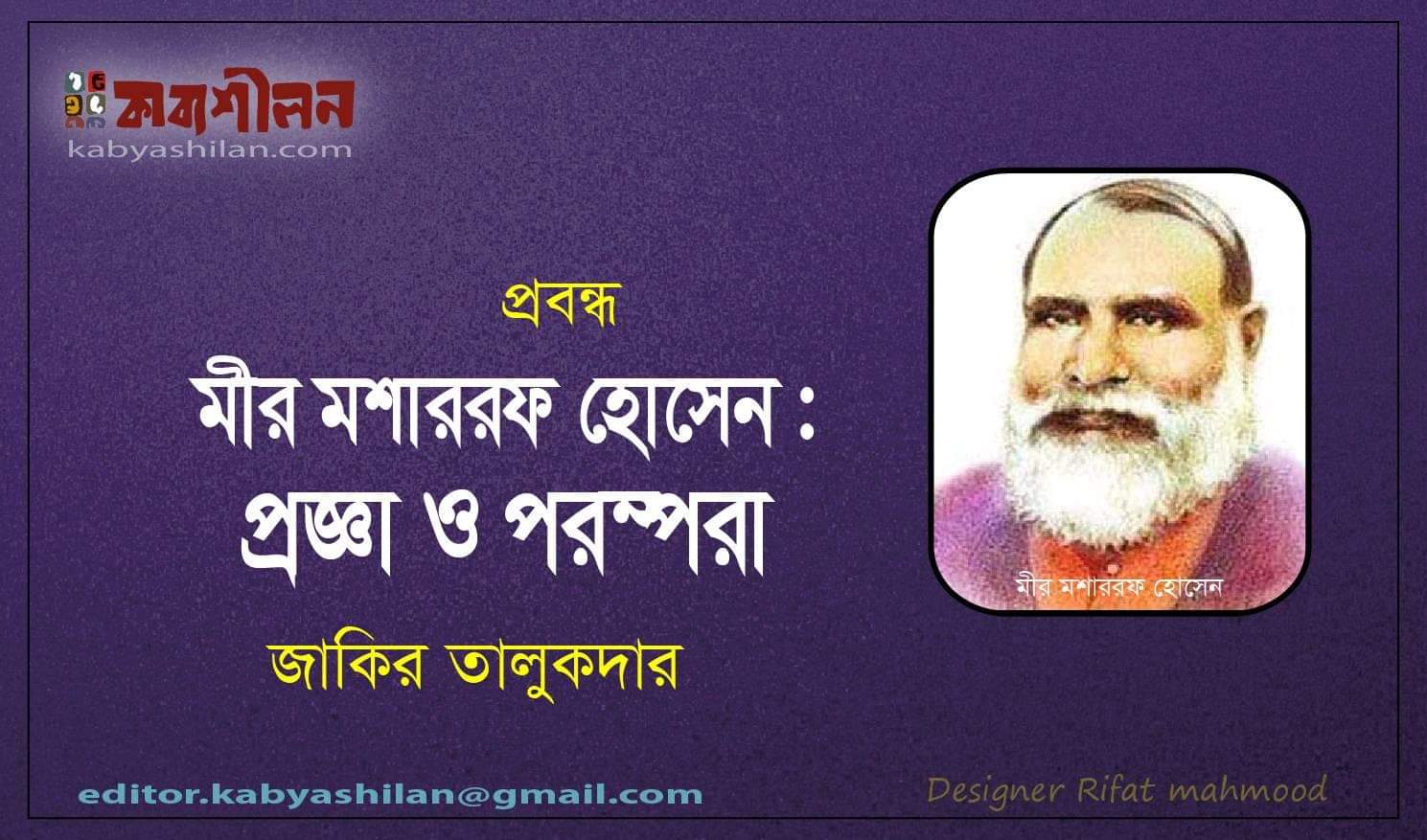প্রবন্ধ।। মীর মশাররফ হোসেন প্রজ্ঞা ও পরম্পরা।। জাকির তালুকদার
মীর মশাররফ হোসেনের রচনা নিয়ে তাঁর জীবৎকালে যেসব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মূল সুর অনেকটাই এক। কী না, কোনো মুসলমান যে এমন সুন্দর বাংলা লিখতে জানেন, মীরের গ্রন্থ পাঠের আগে বাংলার হিন্দু তো বটেই, মুসলমান শিক্ষিত সমাজও নাকি একথা ভাবতেই পারেননি। কাজেই বোঝা মুশকিল যে এইসব আলোচনা কি ব্যক্তি মীর মশাররফের প্রশংসার ছলে তার ধর্মীয় গোষ্ঠীর সমালোচনা, নাকি তাদের সীমাবদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। কারণ যেটাই হোক, ঘুরে-ফিরে একই ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকা এবং সাময়িকীতে। কেউ বলেছেন ‘মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।’ কেউ লিখেছেন ‘এই যে তিন কোটি মুসলমান, বাঙ্গালা দেশই ইহাদের মাতৃভূমি, বাঙ্গালা ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষা। ইহারা যদিও মাতৃভমি বলিয়া অন্য কোন দেশের উল্লেখ করিতে পারেন না কিন্তু পারসী আরবীই তাহাদের মাতৃভাষা মনে করেন। নিন্ম শ্রেণির মুসলমানে কদর্য্য বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা বলিতে বা বাঙ্গালা চর্চা করিতে একান্ত বিরোধী। তাঁহারা অশুদ্ধ উর্দ্দু ছাড়িয়া ভদ্র বাঙ্গালীর সহিত ভদ্র বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ করিতে বড়ই অপমান বোধ করেন, ইহা হিন্দু মুসলমান উভয়ের দুর্ভাগ্যের বিষয়।’ আরেক আলোচক লিখেছেন ‘এই দেশের মুসলমানেরা কেহ যে এরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে জানেন আমরা পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।’ প্রায় একই ধরনের মন্তব্য আরেক পত্রিকায় ‘গ্রন্থখানি যদিও একজন মুসলমানের লিখিত, কিন্তু ইহার ভাষা কিছুতেই মুসলমানের বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুগণেরও বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিতে পারে।’
আবার এই রকম বাংলায় লেখার কারণে নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা মীর মশাররফ যে তিরস্কৃত হয়েছিলেন, সেকথা তিনি নিজেই লিখেছেন ‘বিষাদ-সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে-হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং ইমামদিগের নামের পূর্বে বাংলাভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে।’
মোট কথা ‘বিষাদ সিন্ধু’র মাধ্যমে মীর মশাররফ হোসেন বাংলাসাহিত্যের জগতে একটি আলোড়নই তুলে ফেলেছিলেন। আজকের ভাষায় আমরা বলতে পারি বিষাদ সিন্ধুর আবির্ভাব ছিল সত্যিকারেরই একটি ‘ঘটনা’।
তবে ঘটনাটা এমন ছিল না যে মীর মশাররফ ‘এলেন দেখলেন জয় করলেন’। বিষাদ সিন্দুর আগে রয়েছে দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাস, দীর্ঘ পথচলার ইতিহাস, উত্থান এবং পতনের ইতিহাস, রক্তাক্ত হবার এবং স্বেদাক্ত হবার ধারাবাহিকতা। সকল কবি-সাহিত্যিককেই হৃদয় এবং পদতলের জখম নিয়েও যে পথ পাড়ি দিতেই হয়।
তবে এটি প্রশ্ন হিসাবে সত্যিকারেরই গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে যে, বাংলায় তথাকথিত ‘ ক্ষয়িষ্ণু আশরাফ মুসলমান’ ঘরে জন্ম নিয়ে মীর মশাররফ কীভাবে বাংলাচর্চায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। উদাহরণ তো আরো রয়েছে। যেমন বেগম রোকেয়া। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য মীর মশাররফ। সেই মীর অশুদ্ধ উর্দুর পরিবর্তে কোন দৈববলে বাংলাচর্চায় ব্রতী হলেন?
উত্তর কিছুটা পাওয়া যায় তাঁর ‘আমার জীবনী’তে। দেখা যাচ্ছে লৌকিক বাংলার রীতি-প্রথা তখন তাদের
পরিবারে ঢুকে পড়েছে। জন্মমুহূর্তে শিশুর কানে আজানের বাণী এবং সুর দেওয়া হচ্ছে মুসলিম রীতি অনুসারে। আবার শিশুর শিয়রে রাখা হচ্ছে ভালো কলম, দোয়াত, কালি, সাদা কাগজ, পেন্সিল কাটার ছুরি, ঢোল, তবলা, সেতার, বেহালা, তাস, পাশা, দাবা, লাঠি, সড়কি, তলোয়ার। শিশু যাতে বড় হয়ে সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে, একই সাথে সমর্থবান এবং বীরযোদ্ধাও হয়ে ওঠে, সেই কামনায় শিশুর শিয়রে এইসব জিনিসের যুগপৎ সহাবস্থান।
আরো একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ‘আমার জীবনী’ থেকে। সেটি হচ্ছে ১৮৭২ সালের আদমশুমারির আগে পর্যন্ত বাংলায় যে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা সমান সমান, সেটি কেন জানতেন না বাংলার হিন্দু-মুসলমান কোনো নেতাই। ঐ আদমশুমারির আগে নাম দেখে হিন্দু-মুসলমান আলাদা ভাবে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। মুসলমানদের নাম রাখা হতো গোবরা, পচা, পরাণ, কালো। এমনকি মুসলমান বালকের ডাকনাম থাকত নন্দ, গৌর, কালাচাদ, হরিজন। ভালো নাম মখদুম হলেও ডাকনাম হয়ে যেত মদন। লেখাপড়াজানা মুসলমান হয়তো আদমশুমারির সময় নিজের শুদ্ধনামটি লেখাতেন, কিন্তু অশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের ডাকনাম লিখিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।
মুসলমানের হিন্দুয়ানি নামের ধারাবাহিকতায় মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী কুলসুমের নাম ছিল কালী, আর কুলসুমের মায়ের নাম লালন। আবার নিজে এই প্রবণতার সমালোচনা করেও মীর মশাররফ নিজেও ডাকনামের ক্ষেত্রে এই একই রীতি মেনে চলেছেন। কন্যা রওশন আরার ডাকনাম ছিল সতী। পুত্র ইব্রাহীম হোসেন হন সত্যবান, আমিনা খাতুন কুকি, জমজ দুই বোন ছালেহা এবং সালেমা হয় সুনীতী ও সুমতী, আশরাফ হোসেন হয় রণজিত, ওমর দরাজ হয় সুধন্ব, আর মীর মাহবুব হোসেন হয় ধর্মরাজ।
শহরে পড়াশুনা করতে এসে পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য তাকে আর কি কি করতে হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ আছে একই গ্রন্থে ‘কলেজে ভর্তি হইলাম। কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে। কৃষ্ণনগরের চাল-চলন দেখাদেখি ক্রমে আমার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল। দশজনের আচার-ব্যবহারই আমার অনুকরণীয় হইল। কৃষ্ণনগরে মুসলমানের গৌরবমাত্র নাই। হিন্দুপ্রধান দেশ। ধূতি পরিতে শিখিলাম। চাদর বা উড়ানী গায়ে দেওয়া অভ্যাস হইল। মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাশনেবল করিলাম। হায় হায়! বাউরী চুল কাটিয়া থাক থাক করিলাম। পিছনের দিকে কিছুই নাই। সম্মুখভাগ সিতীকাটার উপযুক্ত মত থাকিল। পাজানা চাপকান বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। টুপিটাও ক’দিন পর সহপাঠিরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল।… পরণ-পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী। চালচলন হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী। মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী, যথা, সামসদ্দীন সতীশ, নাজমুল হক নজু, বোরহান বীরু।’
সাংবাদিকতা ও সম্পাদনাকর্মও তাকে অনেকখানিই সহায়তা করেছে। ১৮৭৪ সালে ‘আজিজন নাহার’ পত্রিকার সম্পাদনা যে তার লেখার পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল, সেকথা তাঁর ঘনিষ্টজনেরা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও বিষাদ সিন্ধু লেখার আগেই লিখে ফেলেছিলেন তিনি অনেকগুলি গদ্য-পদ্য-নাটক-প্রহসন। বিষাদ সিন্ধু প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯১ সালে। কিন্তু তার আগে একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে ‘রতœবতী’ (১৮৬৯), ‘গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু’ ‘বসন্তকুমারী’ ‘জমীদার দর্পণ’ (১৮৭৩), ‘এর উপায় কি?’ (১৮৭৫), ‘সঙ্গীত লহরী’ (১৮৮৭), ‘গো-জীবন’ (১৮৮৯), ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ (১৮৯০)। চূড়ান্ত সিদ্ধি এসেছে বিষাদ সিন্ধুতে। কিন্তু তার আগে তাঁকে বাঙালি পাঠক-সমালোচক-লেখকদের সামনে উপস্থিত হতে হয়েছে আটটি প্রকাশিত গ্রন্থ নিয়ে। সহ্য করতে হয়েছে বিরূপ সমালোচনা, পাঠক-সমালোচকের নীরবতা, যাকে প্রত্যাখ্যান বলেই মনে করেন প্রতিটি লেখক।
এই পথ চলতে চলতেই তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে যে, আশরাফ হোক আর আতরাফ হোক, বাঙালিমাত্রেরই লেখার মাধ্যম হবে বাংলা। ‘বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী?’ এইরকম উদ্ভট প্রশ্নের সমাধান তিনি নিজেই
আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই জীবনটাকে সত্যিকারভাবে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন বাংলাসাহিত্যের সেবার জন্য।
বাংলাভাষায় লেখার জন্য তার সামনে কোন আদর্শ বিরাজমান ছিল তখন? ছিল বঙ্কিমচন্দ্র এবং তার অনুসারী লেখকদের সাহিত্যকর্ম। সমাজের মতো সাহিত্যেও যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যথেষ্ট পরিমাণেই ছড়িয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এক পর্যায়ে হিন্দু লেখকদের হীন প্রবণতায় বিরক্ত হয়ে তাকে একথা বলতেও শোনা গেছে যে ‘পাগল সাজাইতে মুসলমান, আহাম্মক প্রমাণ করিতে হইলে মুসলমান, গালাগালি দিতে হইলেও মুসলমান। ইহার দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে।’
কিন্তু তারপরেও তিনি এই বিশ্বাসে স্থিত থাকতে পেরেছিলেন যে ভাষা আসলে ধর্মনিরপেক্ষ। ভাষাকে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষেও যেমন ব্যবহার করা সম্ভব, তেমনই সম্ভব সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করাও।
সাহিত্য সৃষ্টি করতে এসে, বিশেষ করে উপন্যাস নির্মাণের ক্ষেত্রে, তিনি নির্দ্বিধায় হেঁটেছিলেন
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেখানো পথে। না হেঁটে উপায়ও ছিল না। কেননা হুতোমের পথ গৃহীত হয়নি, গৃহীত হয়নি আলালের ঘরের দুলালের পথও। গৃহীত হয়নি তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্গীয় সারস্বত সমাজের কাছে। গৃহীত হয়েছেন বঙ্কিম। কারণ বাঙালি পাঠকের মনে তখন ইংরেজি নভেলের আদর্শ। আর সেই আদর্শের সাথে মিল পাওয়া গেছে বঙ্কিমের।
তাই বলে মীর মশাররফ হোসেন নিছক বঙ্কিম-অনুকারী ছিলেন না। তা হলে তো আজ তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজনই পড়ত না। বঙ্কিমের চাইতে ভিন্ন কিছু, অন্যরকম কিছু, ছিল মীর মশাররফের। সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেতে হলে প্রবেশ করতে হবে বিষাদ সিন্ধুতে।
কারবালায় নবী-পরিবারের সদস্যদের আত্মাহুতির অব্যবহিত পরেই শোকাবহ এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচিত হতে শুরু করে। ফরজদক এবং হাম্মাদ বিন গালিবের মতো কবিরাও মর্সিয়া লিখেছেন। আরবি ছাড়াও পারস্য, ইরাক, সিরিয়াতে মর্সিয়া লেখা হয়। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে কারবালা নিয়ে ফারসি কবিতা রচিত হয়েছে অসংখ্য। মুহতেশামের ‘হফ্তবন্দ’ এবং কানীর ‘মর্সিয়া’ এই সময়ে রচিত। ভারতবর্ষে উর্দুভাষায় অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে আদিল ও দবিরের মতো কবিরা মর্সিয়া লিখেছেন।
এইসব রচনার সঙ্গে মীর মশাররফ পরিচিত ছিলেন কি না জানা যায় না। তবে তার সময়কালে বাংলাভাষায় অন্তত বারোটি কারবালাকেন্দ্রিক পুঁথি প্রচলিত ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল আবার একজন অমুসলিম কবির (রাধারমণ গোপ) লেখা। পুঁথিগুলি হচ্ছে ‘জয়নালের চৌতিশা’ (শেখ ফয়জুল্লা), ‘‘মাকতুল হোসেন’ (মোহাম্মদ খান), ‘জঙ্গনামা’ (নসরুল্লা খান), ‘আমীর জঙ্গনামা’ (মনসুর), ‘জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব’ (হায়াত মামুদ), ‘জঙ্গনামা’ (ফকীর গরীবুল্লা), ‘জঙ্গনামা’ (সৈয়দ হামজা), ‘শহীদে কারবালা’ (সাদ আলী), ‘শহীদে কারবালা’ (আব্দুল ওহাব), ‘ইমামের জঙ্গনামা’ (রাধারমণ গোপ), ‘হানিফা ও কায়রা পরী’ (শাবিরিদ খান), ‘কারবালা’ (আব্দুল হাকিম)।
এই সবগুলির সঙ্গে না হলেও মীর মশাররফ হোসেন যে অনেকগুলি পুঁথির সঙ্গেই বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ বিষাদ সিন্ধুর অনেক অংশে বা প্রবাহে পাওয়া যাবে।
শেষ পর্যন্ত বিষাদ সিন্ধু তো প্রেম এবং প্রতিহিংসারই আখ্যান। প্রেমপ্রার্থনার উল্টোপিঠেই প্রতিহিংসার অবস্থান
সবসময়ের জন্য স্বতঃসিদ্ধ কি না, তা বলা যায় না। অনেকক্ষেত্রে দুর্বল প্রেমিক বিরহকাতরতাকে সঙ্গী করেই জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এজিদের মতো সর্বার্থেই শক্তিমান এবং অহঙ্কারী পুরুষের জন্য কাতরতা নয়, প্রতিশোধস্পৃহাই বাস্তব। এই প্রেমকামনা, প্রেমাস্পদাকে নিজের করে পাওয়া এবং না পাওয়ার কারণে প্রতিহিংসার আগুনে নিজেকে এবং প্রতিপক্ষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার মনোবৃত্তিটাই লেখকের হাতে উপন্যাসনির্মাণের মূল চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক যতই এটিকে শাস্ত্রানুগ বর্ণনা বলে দাবি করুন না কেন, আদতে শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক এতই আলগা যে সেটিকে অস্বীকার করাটাই ভালো। লেখক বলছেন বটে যে ‘শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ রাখিতে হইতেছে’ কিন্তু আদতে তার লক্ষ ছিল শিল্পসৃষ্টিই। উপন্যাসের মধ্যেই তিনি পাঠককে জানাচ্ছেন যে ‘বিষাদ-সিন্ধুর সমুদয় অঙ্গই ধর্মকাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। বর্ণনার কোনোপ্রকার ন্যূনাধিক হইলে প্রথমত পাপের ভয়, দ্বিতীয়ত মহাকবিদিগের মূলগ্রন্থের অবমানন-ভয়ে তাহাদের বর্ণনায় যোগ দিলাম।’ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষাদ সিন্ধু আদৌ ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক নয়। আবার ইতিহাসের সঙ্গে বিষাদ সিন্ধুর আখ্যানের তেমন কোনো সামঞ্জস্যই নাই। এখানেও কারণ একটাই। মীর মশাররফ হোসেন ইতিহাস লিখতে বসেননি, উপন্যাস লিখেছেন। আর উপন্যাস তো প্রেম, দেশপ্রেম, মনস্তত্ত্ব নিয়েই বেশি কারবার করে। ইতিহাস জানাচ্ছে যে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার আগে ঘটে গেছে অসংখ্য ঘটনা এবং দুর্ঘটনা। সুন্নী ইতিহাসবিদরা এইসব ঘটনাকে আড়াল করেই রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে শিয়া ইতিহাসবিদরা যা লিখেছেন, সেগুলির সঙ্গেও বিষাদ সিন্ধুর কোনো মিল নাই। কারবালার ঘটনারও আগে শুরু হওয়া দ্বন্দ্বই কারবালাতে এসে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। মূলে রয়েছে হাশেমী এবং উমাইয়া পরিবারের দ্বন্দ্ব, নবীর পরিবারের প্রাধান্য নিয়ে সর্বকনিষ্টা পন্থী হজরত আয়েশা এবং প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা হজরত ফাতেমার দ্বন্দ্ব, খিলাফত নিয়ে হজরত আবুবকর এবং হজরত আলীর দ্বন্দ্ব, উমাইয়া বংশীয় তৃতীয় খলিফা হজরত উসমানের বিরুদ্ধে সংঘটিত অভ্যুত্থান এবং হতাকা-ের জের, হজরত আলীর সাথে মুয়াবিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। যে এজিদকে আমরা বিষাদ সিন্ধুতে দেখতে পাই মদ্যপ, অধার্মিক কাফের, দাম্ভিক, খল এবং অত্যাচারী হিসাবে, প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিজীবনে সেই ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমানই। রাজনীতি এবং ক্ষমতার জন্য যতটুকু খারাপ হতে হয়, তারচেয়ে বেশি খারাপ তিনি ছিলেন না। মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরে ইয়াজিদের শাসনকালে সুশাসনের খুব যে অভাব ঘটেছিল, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। প্রথম খলিফার মতোই তাকেও প্রজারা আমীরুল মোমেনিন বা বিশ্বাসীদের সরদার হিসাবেই আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু সেই ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনার কোনো ইচ্ছা তো মীর মশাররফ হোসেনের ছিল না। তিনি যেসব পুঁথি, লোকশ্রুতি থেকে এই উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলিতে ইতিহাস বলতে কেবলমাত্র মানুষগুলির নামই উক্ত হয়েছে। বাদবাকী সবই কবিকল্পনা এবং লোককল্পনা। সেই কারণেই লৌকিক ও অলৌকিক এই উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে। আর উপন্যাসের গুণে এবং পাঠ ও প্রচারের কারণে বিষাদ সিন্ধুকেই প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞান করতে দেখা গেছে লক্ষ লক্ষ স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি মুসলমান নরনারীকে।
সচেতনভাবে পাঠ করতে গেলে এই প্রশ্নটা অবশ্যই মনে জাগে যে বিষাদ সিন্ধু কি লিখন নাকি কথন? আমাদের কি মাঝে মাঝে মনে হয় না যে আমরা আখ্যান শুনছি এক জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী কথনীয়ার মুখ থেকে? আমরা জানি যে লিখিত গল্প সৃষ্টির আগে ছিল গল্পকথনের যুগ। সেই গল্প আবার সকলের বলার বা জানার অধিকার ছিল না। বিশেষ ধরনের মানুষরাই কথক হতে পারতেন। কথকরা গল্প সৃষ্টি করেছেন, মুখ থেকে মুখে সেগুলি ছড়িয়ে পড়েছে পবিত্র আগুনের মতো, তারপর জমা হয়েছে কোনো গোত্রের পুরোহিত কিংবা সবচেয়ে প্রাজ্ঞ মানুষটির বুকে। পৃথিবীতে যত গোত্র, যত কৌম সব গোত্রেই এইভাবে গল্প জন্ম নিয়েছে নিরন্তর। গল্পগুলো জমা থেকেছে গোত্রের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ মানুষটির বুকে। এ যুগের সভ্য মানুষ বিশ্বাসও করতে পারবে না, কী অপরিসীম মূল্য সেই গল্পগুলোর। আমাদের কাছে যতটা, তাদের কাছে তার চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি। কেননা তারা যে আদিম কল্পনার যুগে বাস করত, তাদের জীবনে গল্পগুলো ছিল অতিপ্রাকৃতের প্রতি ভীতির বিরুদ্ধে সাহসের জোগানদার, তাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা। একটি গল্প বা উপাখ্যান পাবার বিনিময়ে যে কেউ নিজের হাতিয়ারটি পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে কথককে। পশুসংকুল মরু-জঙ্গলে কিংবা আদিম জঙ্গলে হাতিয়ার শুধু বীরত্বের স্মারক নয়। তার খাদ্য জোগানোর প্রধান অবলম্বন, তার আত্মরক্ষার একমাত্র কবচ। তবু সে
পুরোহিতকে সেই হাতিয়ারটি দিয়ে দিতে প্রস্তুত একটি গল্পের বিনিময়ে। কেননা তার বিশ্বাস, গল্প হচ্ছে অলৌকিক এক গুপ্তঘরের চাবিকাঠি। সেই চাবিকাঠি হাতে পেলে সে হতে পারবে প্রকৃতির প্রভু। তার ডাকে তখন সাড়া দিয়ে মাথার ওপর ছায়া বিছিয়ে দেবে মেঘ, বৃষ্টি ঝরবে তারই ইচ্ছায়, বনের পশুপাখি হবে তার বশীভূত, তার ইচ্ছাতেই প্রবাহিত হবে বাতাস। এই গল্প তাকে দেবে সেই লুপ্ত চাবি, যা দিয়ে সে খুলে ফেলতে পারবে তার কৌমের প্রজ্ঞার বন্ধ দুয়ার, উদ্ধার করতে পারবে তার টোটেম-চিহ্নের গুপ্তপাঠ। সে তখন আর সাধারণ যোদ্ধা থাকবে না, হয়ে যাবে কৌমের সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব।
এই দেশে, উপমহাদেশে, ইংরেজরা আসার আগে গল্পকথন যে প্রচলিত ছিল সাহিত্যের নানা ধরনের আঙ্গিক হিসাবে, সেই প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। সেই গল্পকথন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল বৃহৎ আখ্যান বর্ণনার দিকে। পাঁচালী, ব্রতকথা, কথকতা যে নিজেদের ধারায় বিকশিত হতে পারলে বাঙালির নিজস্ব উপন্যাস-আঙ্গিকের জন্ম দিতে পারত না, এমন কথা বলা যায় না। সে ভিন্ন বিতর্ক। তবে মীর মশাররফ হোসেন বিষাদ সিন্ধুতে যে কথকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন অনেকখানি তা আমাদের আবহমান কথকতারই পরম্পরা। বারবার তিনি পাঠককে আহ্বান জানাচ্ছেন আখ্যানের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ট হবার জন্য। কখনো আখ্যানে বিরতির যুক্তি দেখাচ্ছেন, কখনো অতিকথনের যুক্তি দেখাচ্ছেন, কখনো মিতকথনের। ‘পাঠক! এতদিন আপনাদের সঙ্গে আসিতেছি, কোনোদিন মনের কথা বলি নাই। বিষাদ-সিন্ধুতে হাসি-রহস্যের কোনো কথা নাই, তন্নিমিত্ত এ-পর্যন্ত হাসি নাই। কাঁদিবার অনেক কথা আছে, থচ নিজে কাঁদিয়া আপনাদের কাঁদাই নাই।’
‘মর্তলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাকে দিতে হইতেছে’ লেখককে। সেই কাজটি মনের মতো করে দিতে পারছেন না বলে কৈফিয়তও দিচ্ছেন তিনি পাঠককেÑ ‘সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে, কল্পনাকুসুমে আজ মনোমতো হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান! সমাজের মূর্খতা দূর করো! আর সহ্য হয় না! যে-পথে যাই, সেই পথেই বাধা।’
মোহাম্মদ হানিফার আখ্যান শুরু করেই আবার মদিনার রওজায় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি পাঠককে। তার পূর্বাভাষও পাঠককে নিজেই দিচ্ছেন তিনিÑ ‘পাঠক! লেখনীর গতি বড় চমৎকার। ষষ্ঠ প্রবাহে কোথায় গিয়াছি, আবার সপ্তম প্রবাহে কোথায় আনিয়াছি।’ নিজের কথন-লেখনীর প্রতি, তথা নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসও প্রকাশিত হচ্ছেÑ পাঠক তাকে ছেড়ে, অর্থাৎ পাঠ ছেড়ে দূরে যেতে পারবেন না।
পাঠককে তিনি শুধু লেখাপাঠই করাচ্ছেন না, দেখিয়ে দিচ্ছেন একের পর এক দৃশ্য। তবে তার আগে নিজে দেখে নিচ্ছেন। কোনো কোনো দৃশ্য দেখতে গিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে তার, জানেন যে এই দৃশ্য দেখলে অন্যেরাও কষ্ট পাবে, তবু দেখাতেই হচ্ছে তাকে ‘হায়! হায়! এ-দৃশ্য কেন চক্ষে পড়িল। উহ্! কী ভয়ানক ব্যাপার। উহ্! কী নিদারুণ কথা! এ-প্রবাহ না লিখিলে কি ‘উদ্ধার-পর্ব’ অসম্পূর্ণ থাকিত, না বিষাদ-সিন্ধুর কোনো তরঙ্গে হীনতা জন্মিত? বুদ্ধি নাই, তাই সিমারের বন্ধনে মনে-মনে একটু সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন যে প্রাণ যায়! এ-বিষাদপ্রবাহে এখন যে প্রাণ যায়! হায়! হায়! এ সিন্ধুমধ্যে কি মহাশোকের কল্লোলধ্বনি ভিন্ন আনন্দ-হিল্লোলের সামান্য ভাবও থাকিবে না? হায় রে কৃপাণ! আবরবণবিহীন কৃপাণ!! এজিদের হস্তে কৃপাণ!!! সম্মুখে মদিনার ভাবী রাজা, ঊর্ধ্বদৃষ্টে দ-ায়মান।’ তবে প্রবাহের শেষ বাক্যটিতে লিখছেন ‘জয়নাল আবেদিনের চিরবিরহে আমাদিগকে কাঁদিতে হইল না। ঈশ্বরের মহিমা!’
আখ্যান বর্ণনা করতে করতে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের ঘোর হঠাৎ কাটিয়ে দিয়ে কথনীয়া মাঝে মাঝে নিজের কথাটুকু বলে নেয়। মূল গল্পে ফেরার আগে দৃশ্যান্তরের আভাস দিয়ে রাখে। কখনো বা আখ্যানের মাঝপথে আখ্যানেরই ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে, বর্ণনা দেয়। মীর মশাররফকেও তা করতে দেখা গেছে বিষাদ সিন্ধুতে। একবার নয়, অনেকবার। যেমন ‘পাঠক! এই অবসরে লেককের একটি কথা শুনুন। সুখের কান্না পুরুষেও কাঁদে, স্ত্রীলোকেও কাঁদে। তবে পরিমাণে বেশি আর কম।… নবীন মহারাজ, তাঁহার মাতার পদধূলি মাথায় মাখিয়া অন্য অন্য গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া বন্দিখানা হইতে বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে
বাজাইতে, জয়পতাকা উড়াইতে উড়াইতে প্রিয় পরিজনসহ রাজপুরীমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করুন; আমরা মোহাম্মদ হানিফার অন্বেষণে যাই। চলুন এজিদের অশ্বচালনা দেখি।’
আবার লেখক যে বিষাদ সিন্ধুর আখ্যানটি শোনাচ্ছেন শোকাবহ ঘটনাটির অনেক শতক পরে, সেকথাও গোপন রাখেন না আখ্যানের মধ্যে। যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি প্রথম হিজরিতে, সেই দূরদর্শন যন্ত্র তুলে দেন এজিদের সেনাপতি ওতবে অলীদের হাতে। কেননা এটা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যাবে ভালোভাবে। অলীদের জবানীতে পর্যবেক্ষণ, মানে লেখকেরই পর্যবেক্ষণ। দেখাটা তাই অলীদের নয়, লেখকের নিজের জন্যই প্রয়োজন।
বিয়ের সময়ে প্রদত্ত দেনমোহরের প্রসঙ্গে লেখক একেবারে তার সমসাময়িক ব্রিটিশ-ভারতে চলে এসেছেন উপন্যাসের মধ্যেই, কোনো ফুটনোট ব্যবহার ছাড়াই। ‘অধুনা যে-প্রকার লক্ষ লক্ষ টাকার দেনমোহর ভারতের মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, যে-প্রথানুসারে স্বামীর যথাসর্বস্ব কন্যার কোক্ষগত করিয়া স্বামীকে পথের ভিখারি করা হইতেছে, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। ব্রিটিশবিধিও এই ধর্মসংক্রান্ত এবং শাস্ত্রসঙ্গত।’
জানিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি ভারতে তথা বাংলায় বসে মদিনা-দামেস্ক, কারবালার গল্প শোনাচ্ছেন। উপন্যাসের মধ্যেই বলছেন ‘ভারতের ন্যায় তথা পালকি বেহারা নাই।’
জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যিকমহলে কিছুটা অস্বস্তি বিরাজ করে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা কাজী নজরুল ইসলামের উদাহরণ সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি না যে একই সঙ্গে একজন লেখকের পক্ষে বড় লেখক এবং জনপ্রিয় লেখক হওয়া সম্ভব। কিন্তু যুগের পরিবর্তন, শতাব্দীর পরিবর্তন, মূল্যবোধের পরিবর্তন, মানুষের রুচির পরিবর্তন সত্ত্বেও যখন একটি গ্রন্থ স্বকীয় উজ্জ্বলতা নিয়ে পাঠকের হৃদয়ে বিরাজিত থাকে, নতুন পাঠককেও কাছে টেনে নিতে সক্ষম হয়, তখন সেই গ্রন্থ অবশ্যই আলাদাভাবে চিন্তার ও মূল্যায়নের দাবি রাখে।
আমরা জানি যে বিষাদ সিন্ধু মীর মশাররফ হোসেনের পরিণত বয়সের ফসল। তিন পর্বে বিভক্ত এই উপন্যাস সাত বছর সময় নিয়ে রচিত হয়েছিল। প্রথম পর্ব প্রকাশের সময় লেখকের বয়স ৩৬ বছর, আর শেষ পর্ব প্রকাশের সময় বয়স ৪২ বছর। বয়সটি শিল্পসৃষ্টির জন্য সবচাইতে উপযুক্ত বয়সসীমার অন্তর্গত। পুঁথির সাথে তার পরিচয় ছিলই। আবার কৈশোরেই তিনি তারাশঙ্কর তর্করত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। সাংবাদিকতার সূত্রে যোগাযোগ ঘটেছিল ঈশ্বর গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ‘সম্বাদ প্রভাকর’ পত্রিকার সাথেও। কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্যের যে প্রকরণ এবং প্রবণতার বিস্তার ঘটেছিল ঐ সময়, সেই ধারার সাথে পরিচিত হতে পারা মীর মশাররফের জন্য মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। তিনি জেনেছিলেন যে ইতিহাস নয়, ধর্মতত্ত্ব নয়, তাকে লিখতে হবে উপন্যাস। আর সেই উদ্যোগের ফসল বিষাদ সিন্ধু। প্রেম-প্রত্যাখ্যাত, প্রেমবঞ্চিত দুই নর-নারীই এই উপন্যাসের মূল ব্যক্তিত্ব। একজন এজিদ, অপরজন জায়েদা।
এজিদের জবানীতে সেই অসহায়তা, যা একজন কাতর প্রেমিকের কণ্ঠেই বেজে উঠতে পারে ‘হা! কী কুক্ষণেই জয়নাব-রূপ নয়নে পড়িয়াছিল! সেই বিশালাক্ষীর দোলায়মান কর্ণাভরণের দোলায় কী মহা-অনর্থই ঘটিল! অকালে কত প্রাণীর প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর হইতে একেবারে উড়িয়া চলিয়া গেল! শত শত নারী পতিহারা হইয়া মনের দুঃখে আত্মবিসর্জন করিল! কত মাতা সন্তানবিয়োগে অধীরা হইয়া অস্ত্রের সহায়তায় দৈহিক মায়া হইতে শোকতাপের যন্ত্রণা হইতে আত্মাকে রক্ষা করিল! কত দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান একবিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতার ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হইল! ছি! ছি! সামান্য প্রেমের দায়ে, দুরাশার কুহকে, মহাপাপী হইতে হইল! হায়! হায়! রূপজ মোহে মোহিত হইয়া আত্মহারা, বন্ধুহারা, শেষে সর্বস্বহারা হইতে হইল! বিনা দোষে, বিনা কারণে কত পুণ্যাত্মার জীবনপ্রদীপ নিবিয়া গেল! এত হইল, এত ঘটিল, তবু আগুন নিবিল না।’
জায়েদার কার্যের পেছনের কারণ সেই জয়নাব। প্রকাশও অনেক বেশি তীব্র ‘তোকে কাঁদাইতেই এ-কাজ করিয়াছি। যদি স্বামীকে ভালোবাসিয়া থাকিস তবে আজ কেন চিরকালই কাঁদিবি! চন্দ্র, সূর্য, তারা, দিবা, নিশি সকলেই তোর কান্না শুনিবে। তাহা হইলেই কি তোর দুঃখ শেষ হইবে? তাহা মনে করিস না। যদি জায়েদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস জায়েদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত? শুধু তোকে কাঁদাইয়াই ছাড়িব না। আরো অনেক আছে। এই তো আজ তোরই জন্য পাপীয়সী কেবল তোরই জন্য জায়েদা এই স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।’
উপন্যাসের এমনি গুণ যে শেষ পর্যন্ত মনেই থাকে না, যে যা কিছু ঘটেছে, সবই ঈশ্বরের লিখনেই ঘটেছে। উপন্যাসের শুরুতেই নবীর কাছে স্বর্গীয় দূত যা ঘটবে বলে জানিয়ে গেছেন, সেগুলোই ঘটেছে। গ্রিক ট্রাজেডির মতো মানুষের সকল চেষ্টা-প্রতিরোধ-বীরত্ব নিষ্ফলই হয়েছে। কিন্তু পাঠক লেখকের ইশারা অনুসারে এজিদকে দায়ী করেন, জায়েদাকে দায়ী করেন, মায়মুনা-সিমার-মারওয়ানকে ঘৃণা করেন, হাসান-হোসেনের জন্য চোখের পানি ফেলেন, আবদুল ওহাব, মসহাব কাক্কা, আলী আকবর, কাসেম, ওমর আলী, সর্বোপরি মোহাম্মদ হানিফার বীরত্বে বিমোহিত হন, সকিনার দুঃখে বুকফাটার কষ্ট অনুভব করেন, জয়নাল আবেদিনের নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। মীর মশাররফ হোসেন পাঠককে দিয়ে যা করাতে চেয়েছেন, পেরেছেন। একজন লেখকের এরচেয়ে বেশি চাই কী?